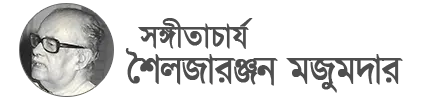শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভাশুর। আমি তাঁকে বড়দা বলে ডাকতাম। আমার বাবা এবং বড়দা একদম একই বয়েসের, দুজনেরই উনিশশো সালে জন্ম। সেজন্য আমি বড়দাকে বাবার মতই দেখতাম, এবং উনিও আমাকে মেয়ের মতই দেখতেন।
বড়দারা ছিলেন সাত ভাই এক বোন, আমার স্বামী দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। বাবা রমণীকিশোরের মৃত্যুর পর বড়দাই ছিলেন এই পরিবারের অভিভাবক। আমাদের বিয়েতে কনে পছন্দ করা থেকে বিয়ের আয়োজন সব তিনিই করেছিলেন। বড়দার নিজের মাসী ছিলেন আমার মায়ের আপন কাকীমা। শুনেছি বড়দা তাঁকে বলেছিলেন মানিকের (মানে তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার এর) বিয়ে টা আমি একজন সিলেটী মেয়ের সঙ্গে দিতে চাই আর সে গান জানা মেয়ে হতে হবে। এমন মেয়ে কি তুমি খুঁজে দিতে পার? মাসী বললেন আমার জানা এক সিলেট এর ডাক্তার এর মেয়ে আছে যে গানে খুব নাম করেছে। সে ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত গান গায় আর তার নাম কাগজে বেরোয়। বড়দা নাকি একবাক্যে রাজি হয়ে গেছিলেন। বিয়ের আগে তাঁরা আমাকে দেখতেও চাননি। আমি কিন্তু তখন বিয়ের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না বরং খুব আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমার বাবা বোঝালেন গানের বাড়িতে বিয়ে হলে আমার গান শেখা এবং অনুষ্ঠান করা বজায় থাকবে এবং আমার পদবি দত্তই থাকবে – তখন আমি রাজী হলাম। আমার বাবা খুব ভুল করেননি, এরকম শ্বশুরবাড়ি পাওয়া ভাগ্যের কথা।
১৯৫৬ সালে আমাদের বিবাহ হয় এবং বিয়ের পর বড়দা আমাদের জন্যে শান্তিনিকেতন এ চীনা ভবনে একটি বিশেষ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। আজও মনে আছে সেখানে রবিঠাকুরের ভাইঝি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দুজন কে দুপাশে বসিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন আর দুটি বাটিকের উত্তরীয় পরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা যে আমার কত বড় পাওয়া তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
বিয়ের পর আমরা গড়পারের একটি বিশাল পাঁচতলা বাড়ির তিনতলায় এসে উঠি। সেখানে আমার দুই ভাশুরের পরিবার আর বড়দা থাকতেন। আরেক ভাশুর সুনীল সেজদা এবং তাঁর স্ত্রী, কণিকা মজুমদার নামে যাঁকে সবাই চেনে, তাঁরাও সেখানে থাকতেন। আমি নতুন বৌ, তায় সবার চেয়ে ছোটো, তাই সব ভাশুর ও জায়ের খুব আদরের ছিলাম। বড়দার সঙ্গে তখন অনেকেই দেখা করতে আসতেন আর বেশির ভাগ সময়ে আমার ডাক পড়ত। বড়দা তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেন। তখন আমি ঘোমটা মাথায় দিয়ে যেতাম কিন্তু ঘোমটা মাথায় দিতেই হবে এমন কোনো নিয়ম আমার জন্যে ছিলনা, যদিও আমার অন্য জায়েরা ভাশুরদের সামনে ঘোমটা দিয়েই যেতেন।
কাজের লোক ছিল, কিন্তু রান্না টা আমার সেজ জা ই করতেন। আমাকে আমার জায়েরা কোনো কাজ করতে দিতেন না, শুধু বলতেন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। তবে পরিবেশনের কাজটা আমার করতে খুব ভালো লাগত। দোতলার বারান্দায় পিঁড়ি পেতে সব ভাইরা একসঙ্গে বসে খেতেন। পরিবেশন করতে গিয়ে দেখলাম ময়মনসিংহের লোকেরা ডালটা সবার শেষ পাতে খান। খুব অবাক লেগেছিল কারণ আমরা সিলেটে এরকম কখনো দেখিনি।
ওঁরা ভাইরা সকলেই খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। যখন একত্র হতেন তখন হাসি মজায় বাড়ি ভরিয়ে তুলতেন। আমার সামনে ইচ্ছে করে শুদ্ধ ময়মনসিংহের ভাষায় কথা বলতেন আর আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না। খাবার সময়েই এসব মজা হত, বাকি সময়ে অবশ্য গাম্ভীর্য বজায় রেখে খুব পরিশীলিত ভাষায় কথা বলতেন। আরেকটা জিনিষ আমার খুব ভালো লেগেছিল – এই পরিবারে সব পুরুষ রা স্ত্রীদের খুব মর্যাদা দিতেন ও তাঁদের মতামত নিয়ে চলতেন। কাউকে কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি।
একবার সাহস করে বড়দা কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার ভাইরা সবাই নিজের পদবী দত্ত মজুমদার লেখেন, কিন্তু আপনি দত্ত টা বাদ দিয়েছেন কেন? বড়দা বলেছিলেন নামটা খুব লম্বা হয়ে যায়।
গড়পারের বাড়িটা রেনভেট করানো হবে বলে আমাদের ছেড়ে দিতে হল। তখন সব ভাইরা আলাদা আলাদা বাড়িতে উঠে যান।
১৯৬১ সালে বড়দা সঙ্গীতভবনের কাজ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে চলে আসার পরের বছর আমার স্বামী, বড়দা ও আমার বড় মেয়েকে নিয়ে আমরা কলকাতায় খ্রিস্টোফার রোডের সি আই টির একটি ছোটো ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করি। ঝুমাকে আড়াই বছরের নিয়ে এসেছিলাম। এখানেই আমার ছোট মেয়ে বুলুর জন্ম হল। দুটি ঘরের ফ্ল্যাট, একটিতে বড়দা অন্যটিতে আমরা। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল খুব সাধারণ কিন্তু disciplined. আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি গোল টেবিল ও চেয়ার, যেটা খাবার এবং লেখাপড়ার জন্যে ব্যাবহার হত। জানলার খোপে অঁর এস্রাজটা দাঁড় করানো থাকত। বাড়ীতে বড়দার একটা ট্রান্সিস্টর ছিল, সেটাতেই সবাই মিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসর শুনতাম সকালে আর দুপুরে। বড়দা সব গান খুব মন দিয়ে শুনতেন আর পরে গানের ক্লাসে সেগুলি নিয়ে মন্তব্য করতেন।
আমাদের দুই মেয়েকে বড়দা খুব স্নেহ করতেন আর আদর করতেন। ঝুমার ভালো নাম রাখলেন অনুত্তমা আর বুলুর নাম রাখলেন অনুষঙ্গা – তবে আদর করে ঝুমাকে ডাকতেন তাকুনু আর বুলুকে ডাকতেন মুনু বলে। ওঁর ছোট ভাই, আমার স্বামী, দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার যখন office চলে যেতেন তখন আমি বড়দার কাছে বাচ্চাদের রেখে রান্নাবান্না আর স্নান সেরে নিতাম। বুলু তখন খুবই ছোট, উনি তাকে পেটের ওপর তুলে নাচাতেন আর গান করতেন। বড়দার ছোট ভাই ওঁর ব্যাংক এবং বাইরের সব কাজ করে দিতেন আর আমি ঘরের কাজ করতাম। ওঁর খাওয়ার অনেক নিয়ম ছিল, ঠিক সময়ে ঘড়ি ধরে খাবার দিতে হত। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই বেলের শরবত খেতেন আর সেই বেল আসত কে সি দাসের বাড়ি থেকে। তারপর সকাল ঠিক আটটায় breakfast করতেন। প্রথমে cornflakes খাওয়া হলে বাটি সরিয়ে নিয়ে অন্য প্লেটে পাউরুটি, ডিম, কলা আর মিষ্টি দিতে হত। সবশেষে চা।
সকাল দশ টার পর থেকে ছাত্র ছাত্রী আসা শুরু হয়ে যেত। ঐ ছোটো ঘরটিতেই রোজ গান শেখানোর আসর হত, এবং কত শিল্পী যে আসতেন তাঁর কাছে গান শিখতে বা রেকর্ডিং করার আগে দেখিয়ে নিতে। পাড়ার লোকেরা আমাদের বাড়িটাকে চেনাত গানের বাড়ী বলে। আমাকে বড়দা বলেছিলেন তুমিও ওদের সঙ্গে বসে যেও আর যে গান টি তোমার আলাদা করে শেখার ইচ্ছে, সেটা যেদিন কেউ আসবেনা সেদিন আমি শিখিয়ে দেব। সেভাবেই আমি ‘তুমি কিছু দিয়ে যাও’ এবং টপ্পার অনেক কঠিন গান শিখেছিলাম। স্পর্শ সুর লাগালে আর ছোট ছোট টপ্পার কাজ লাগালে যে গান এত সুন্দর হয়, তাও ওঁর কাছে শিখেই উপলব্ধি করেছি। উনি বলতেন সূক্ষ্ম কাজ হারমোনিয়াম এ আসেনা, তাই এস্রাজ ও তানপুরা দিয়েই গাওয়া পছন্দ করতেন। তবে ওঁর শালী কুইনিদি যখন গাড়ি করে হারমোনিয়াম নিয়ে গান শিখতে আসতেন তখন কিন্তু আপত্তি করতেন না। কত বড় বড় শিল্পী দের ওই বাড়িতে আসতে দেখেছি। দুপুর দুটো – আড়াইটে বেজে যেত – তখনও গান চলছে। দুপুরের খাবার খেতে অনেক দিনই বেশ দেরি হয়ে যেত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, আমার ও হারমোনিয়াম নিয়ে গান করার অভ্যাস ছিল, কিন্তু বড়দার ভয়ে আমার হারমোনিয়াম টা বারান্দায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। অনেক বছর পরে বৃষ্টিতে অযত্নে সেই হারমোনিয়াম টা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে গান শেখাবার সুবিধের জন্যে যখন আরেকটা হারমোনিয়াম কিনতে হল, বড়দা আর আপত্তি করেন নি।
একটা কথা এখানে বলা দরকার – আমার ভাশুরদের ছেলেমেয়েরা সবাই বেশ ভালো গান গাইতে পারত, কিন্তু বড়দা তাদের কোনোদিন গান শেখাবার কথা ভাবেন নি। তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অনেক বেশী মন দিয়েছেন, নিজের পরিবারের মধ্যে যে talent আছে তাদের একটু বরং উপেক্ষাই করেছেন। আমার ভাশুরপো রা আমার কাছে এসে গান শিখত, জ্যাঠামশায়ের কাছে যাবার সাহস পেত না।
বিকেল বেলা প্রায়ই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান বা rehearsal থাকত। মঞ্জু দের বাড়ি থেকে গাড়ি আসত ওঁকে নিয়ে যাবার জন্য। চা খাওয়া হয়ে গেলেই বলতেন নেলি, তৈরি হয়ে নাও। সব অনুষ্ঠানেই আমাকে নিয়ে যেতেন আর ফেরার সময় আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানের গান পরিবেশনা ও চয়ন নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করতেন। তখন আমিও কত মতামত দিতাম আর উনি আমার মত সাধারন মানুষের মত কেও মূল্য দিতেন। এখন বুঝি আমার কত বড় ভাগ্য যে ওঁর সঙ্গে এসব আলোচনায় যোগ দিতে পেরেছি।
আমাদের কয়েকজন শিল্পী দের নিয়ে বড়দা রবিরঞ্জনী সংস্থা তৈরি করেছিলেন, প্রধানত কোরাস গান গাইবার জন্য। সেই সংস্থায় দুজন বুলবুল ছিল – একজন বুলবুল সেনগুপ্ত আরেকজন বুলবুল বসু। আর ছিল আশিষ, উৎপল, এনাক্ষী, শ্যামশ্রী, আরেক নমিতা – নমিতা ঘোষ, চিত্রা চ্যাটার্জী ইত্যাদি। আমরা একসঙ্গে অনেক রেডিও প্রোগ্রাম আর stage এ অনুষ্ঠান করেছি। বুলবুল বসু র সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেকদিনের – আজও সেই বন্ধুত্ব অটুট আছে।
আগেই বলেছি বড়দার সব কাজ আমি করতাম। একবার বিছানা তুলতে গিয়ে দেখি বালিশের নীচে মিষ্টির বাক্স। ওঁর diabetes ছিল, তাই K. C Das এর বাড়ি থেকে মঞ্জু ওঁর জন্য diabetic special সন্দেশ পাঠাত। উনি সেগুলো বালিশের পাশে রেখে দিতেন ও মাঝে মাঝে খেতেন। আমার তো খুব ভয় হল বিছানায় পিঁপড়ে ধরে যাবে – আর আমি বলতেও পারব না সরাতেও পারব না। রোজ খুব সাবধানে বিছানা পরিষ্কার করে রাখতাম যাতে পিঁপড়ে না ধরে। আশাকরি উনি কোনোদিন জানতে পারেন নি যে আমি দেখে ফেলেছি।
একটা মজার কথা মনে পড়ছে। আমি সি আই টির ফ্ল্যাটে আসার পর বালীগঞ্জের গীতবিতানে সেকেন্ড ইয়ার এ ভর্তি হয়েছিলাম। শ্রী নীহারবিন্দু সেন আমাদের থিওরি পড়াতেন আর শ্রীমতী গীতা সেন গান শেখাতেন। ফিফথ ইয়ার এর শেষে যখন ফাইনাল পরীক্ষা হবে তখন জানলাম যে আমাদের External Examiner হয়ে আসবেন শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার। পরীক্ষার একটা বিভাগ ছিল স্বরলিপি র ওপর। Examiner এক লাইন গান গাইবেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরলিপি তৈরী করতে হবে। আমি যদিও স্বরলিপি ভালই পড়তে পারতাম, কিন্তু বড়দার সামনে ঠিক মনের কী অবস্থা হবে সেটা নিয়ে খুব টেনশন হতে লাগলো। বাড়ি তে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে কথাটা মনে হতে লাগলো। পরীক্ষার দিন এগিয়ে এলে একদিন নীহারদা আমায় ডেকে বললেন শৈলজাদা বলেছেন উনি তোমার পরীক্ষা নেবেন না। একজন ক্লাসিকাল গাইয়ে তোমার পরীক্ষাটা নিয়ে নেবেন। তখন আমার স্বস্তি হল।
গীতবিতান থেকে গীতভারতী উপাধি পাবার পর আমি অনেক অনুষ্ঠান করেছি বড়দার পরিচালনায়। একবার প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী শ্রী বসন্ত সিং এর একটি অনুষ্ঠানে বড়দা আমাকে দিয়ে ‘চিত্ত আমার হারালো আজ ‘ গানটি solo গাইয়েছিলেন আর তার সঙ্গে শ্রীমতী অনুরাধা রায় কে দিয়ে নাচ করিয়েছিলেন।
আমার মেয়েরা একটু বড় হলে বড়দা আমায় বললেন তুমি প্রত্যেক রবিবার সুরঙ্গমায় আমার Special class টা এটেন্ড করো। Special Class এ উনি টপ্পা আর ধামারের কঠিন গানগুলি শেখাতেন, আর পাখোয়াজের সঙ্গে practice করাতেন। আমি সকালবেলা বড়দাকে ব্রেকফাস্ট তৈরী করে দিতাম। উনি তারপরই সুরঙ্গমায় চলে যেতেন। আমি দুপুর আর রাত্রের রান্না সেরে দুবার বাস বদলে রাসবিহারী রোডের সুরঙ্গমায় পৌঁছোতাম। সেই সময় আমার স্বামী, যাঁকে সবাই মাণিকদা বলে চেনে, তিনি সুরঙ্গমায় ক্লাসিকাল গান শেখাতেন। আমাদের ক্লাস শেষ হলে আমরা তিনজন একসঙ্গে বাড়ী ফিরতাম। ফিরেই খাবার গরম করে সবাইকে পরিবেশন করতাম। খাবার দিতে একটু দেরী হলেও কখনো কিছু বলেননি।
বড়দা কে কখনো সংসার ধর্ম ও দেশের রাজনীতি নিয়ে ভাবতে বা কথা বলতে দেখিনি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ই ছিল ওঁর ধ্যান জ্ঞান। বড়দা ছাত্র ছাত্রীদের আর আত্মীয় স্বজন দের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে থাকতে ভালোবাসতেন – যেখানেই যেতেন সেখানে তাঁর গানের ক্লাস বসে যেত। আমাদের বাড়ি থেকে উনি ওঁর এক ভাই প্রবোধরঞ্জন, আমাদের চিনিদার বাড়ি কনভেন্ট রোডে কিছু বছর ছিলেন। শেষ জীবন তাঁর কেটেছে আরেক ভাইয়ের বাড়িতে, সল্ট লেক এ। আমাদের C I T building এর বাড়িতে যে ষোল – সতেরো বছর তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেই স্মৃতি আমার মনে গাঁথা আছে। আমি তখন একা হাতে রান্নাবান্না আর সংসার সামলেছি, দুই মেয়েকে বড় করেছি এবং গানের জগতে নিজেকে ঢেলে দিয়েছি। বড়দা ও আমার স্বামী কখনোই আমাকে সংসারে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেননি বরং উৎসাহ দিয়েছেন নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। ওঁর তানপুরা আর স্বরলপির বই গুলো আমাকে দিয়ে গেছেন – সেগুলো আজও আমার সঙ্গী। শৈলজারঞ্জনের ভাইদের পরিবারের এই প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে এখন কেবল আমিই রয়েছি, পুরোনো স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে।