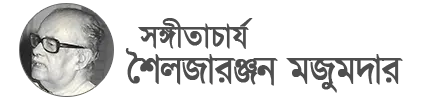পূর্বকথা
রমণীকিশোর মজুমদার ও সরলাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলজারঞ্জন মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন ইংরেজী ১৯০০ সালের ৮ঠা শ্রাবণ অখন্ড বাংলার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বাহাম নামক গ্রামে। পিতা রমণীকিশোর ছিলেন নেত্রকোনা শহরের ডাকসাইটে উকিল, জীবনে খুব কম মামলাতেই হার মেনেছেন । মোহনগঞ্জে কংসনদীর সমীপবর্তী অঞ্চলে তাঁদের ছোটখাটো জমিদারী ছিল, তার দেখাশোনা করতেন রমণীকিশোরের মাতা সৌদামিনী দেবী। শিক্ষিতা ও সুগায়িকা সৌদামিনী দেবী নিজে গান গাইতেন, রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচিতা ছিলেন। জমিদারীর কাজও তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন।
রমণীকিশোরের কথা থেকে জানা যায় এঁদের বংশের পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব থেকে এসে বর্ধমানে স্থিত হয়েছিলেন। প্রথম প্রজন্ম বর্ধমানের রাজার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বর্ধমানের রাজা এঁদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ময়মনসিংহে জমি প্রদান করেছিলেন। তৃতীয় প্রজন্ম থেকে এঁরা ময়মনসিংহে বসবাস করতে শুরু করেন। বাহামের দত্ত মজুমদার বাড়ির চার ভাগ ছিল। দক্ষিণাবাড়ির অংশ রমণীকিশোর ও ভ্রাতা তারাকিশোর মজুমদারের অংশ । পুবের বাড়ির অংশ ছিল পূর্ণচন্দ্র মজুমদার এবং দুর্গাদাস মজুমদারের। উত্তরা বাড়ির অংশ ছিল কানু মজুমদারের। পশ্চিমা বাড়ি খুব তাড়াতাড়ি নির্বংশ হয়ে যায়।
দত্ত মজুমদার বাড়ির বিগ্রহ গোপাল – এক পুরোহিত সেই বিগ্রহ বেনারস থেকে এনেছিলেন। চল্লিশ বছর এ বাড়িতে থাকার পর তিনি নিজের জমি পূর্ণচন্দ্র দত্ত মজুমদার কে বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যান। অতঃপর বাহামের নিকটবর্তী বলসি গ্রাম থেকে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীকে আনিয়ে পুরোহিতের কাজে বহাল করা হয়, এবং পূর্ণচন্দ্র তাঁর জমিটা ঈশ্বরচন্দ্র কে দান করেন। সেই দেবোত্তর জমি ঈশ্বরচন্দ্রর বংশধরেরা আজ ও ভোগ করছেন। মন্দিরে বিগ্রহ কিন্তু আজ আর নেই । পুরোহিতের বংশধরেরা বলেন ১৯৭১ এর সংগ্রামে বাড়ি লুঠপাট হয়ে যায় , তখনই বিগ্রহটিও চুরি যায় । গ্রামের লোকেরা বলেন বিগ্রহটি বেচে দেওয়া হয়েছে।
যতদূর জানা যায় রমণীকিশোর ও তারাকিশোরের পিতা চন্দ্রকিশোর এঁদের শৈশবেই মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী দেবী সংসার ও জমিদারীর হাল ধরেন। রমণীকিশোর দুঁদে উকিল হলেও সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। একবারের মামলায় উপার্জন করা টাকা যতক্ষন না ফুরাত ততক্ষণ তিনি আদালতে যেতেন না। যেদিন তিনি আদালতে যেতেন সেদিন ভীড় উপছে পড়ত তাঁর সওয়াল করা দেখার জন্যে। কলকাতা থেকে নামকরা ব্যারিস্টার এসেও তাঁকে হারাতে পারতেন না। তাঁর অসাধারণ মেধা ছিল – তাঁর শ্রেণীতে প্রথম হওয়া ছাত্রকে তিনি বাজী রেখে হারিয়েছেন একটাও বই না কিনে, বরং তারই বই অবসরমত চেয়ে নিয়ে।
সংগীতের প্রতি অনুরাগ
পিতা রমণীকিশোর কিন্তু গান বাজনা একেবারেই পছন্দ করতেন না। শৈলজার গলায় সুর আছে দেখে শিক্ষকেরা যখন তাঁকে দিয়ে স্কুলের অ্যানিভারসারিতে একটি প্রার্থনাসঙ্গীত গাওয়াবেন স্থির করেন তখন রমণীকিশোর কিছুতেই মত দেননি ছেলে বখে যাবার ভয়ে। নেত্রকোনা শহরে যাত্রা এলে সেখানেও ছেলেদের যাওয়া বারণ ছিল। এ হেন গান বিদ্বেষী বাড়িতে গানের ধারা ফল্গুধারার মত বইছিল শৈলজারঞ্জনের ঠাকুমা সৌদামিনীর মাধ্যমে। তিনি বৈষ্ণব গান করতেন, রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে ভালোবাসতেন। শৈলজার গানের হাতেখড়ি ঠাকুমার কাছেই। তাঁর একটা বক্স হারমোনিয়াম ছিল , তাই বাজিয়ে গান করতেন ও তাঁর আদরের শৈলকে রাধাকৃষ্ণের গান শেখাতেন। মাঠে চাষিরা ধান কাটতে কাটতে গান গাইত , সেই সুর শৈলজার মনে থেকে যেত। কীর্তনের আসরের মধ্যে বসে অনেক গান শুনতেন , সেগুলো ও মনে দাগ কাটত। যে গান ভালো লাগত সেটাই গলায় তুলে নিতে পারতেন ছোটো বয়েস থেকেই। রবীন্দ্রনাথের কিছু গান শুনে ভালো লেগেছিল , গলায় তুলে নিয়েছিলেন , কিন্তু সবার সামনে গাইতে কুন্ঠিত বোধ করতেন – খানিকটা আত্মবিশ্বাসের অভাবে আর খানিকটা তখনকার আশেপাশের লোকেদের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বিরূপতার জন্যে। অনেকেই তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বোঝার চেষ্টা করতেন না আর গাইবার ধরণকে ‘ন্যাকামী’ মনে করতেন। বোন প্রতিমার ও গানে আগ্রহ ছিল। শৈলজা তাকে একটি এস্রাজ কিনে দিয়েছিলেন।
রমণীকিশোর যখন ওকালতি করতে শুরু করেন তিনি পরিবার নিয়ে নেত্রকোনা শহরে চলে আসেন, কিন্তু সৌদামিনী দেবী গ্রামেই থেকে যান। শেষ জীবন তাঁর কাটে বৃন্দাবনে। নেত্রকোণায় ছুটির সময় শৈলজার চার জ্ঞাতি খুড়তুতো কাকা ভবেশ, সুরেশ, বাড়ি আসতেন আর পাঠভবন, শান্তিনিকেতন আশ্রমের গল্প করতেন। সেই গল্প শুনে ছোটবেলা থেকেই মনে শৈলজার মনে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটা মুগ্ধতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় সেই চার কাকার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয় এবং জোড়াসাঁকো এবং রবীন্দ্রনাথের কথা আবার করে কানে আসে। সে সময় অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রসংগীত – এই দুই ধরণের গান খুব জনপ্রিয় ছিল। শৈলজা কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় সারদারঞ্জনের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন, কিন্তু মন পড়ে থাকত ঠাকুমা সৌদামিনীর আপন ভাই উপেন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে। উপেন্দ্রর বড়ো ছেলে চারুচন্দ্র চৌধুরীর কাছে শৈলজা প্রথম শুনলেন রবীন্দ্রনাথের গীতপঞ্চাশিকার গানগুলি – ‘আমার নিশীথরাতের বাদলধারা’, ‘কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে’ প্রভৃতি। সেই গান শোনার পর শৈলজার মনে হল এ যেন অন্য জগতের গান। চারুচন্দ্রের কাছ থেকেই শিখলেন কি করে স্বরলিপি থেকে গান তুলতে হয়। তখন হারমোনিয়ামে দক্ষতা অর্জন করলেন এবং নানান জায়গা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথের গান তখন তাঁর মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছে। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তণী শিবদাস রায় এর সঙ্গে নিজেই আলাপ করে তার কাছ থেকে কিছু রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে শীতল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি এস্রাজ শিক্ষা লাভ করেন। সেই শিক্ষা তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনে খুব কাজে লেগেছিল।
গানের নেশায় শৈলজারঞ্জন বহুকষ্টে ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবের কার্ড জোগাড় করতেন। শৈলজারঞ্জন প্রথম জোড়াসাঁকোয় যান ১১ই মাঘের উৎসবে । সেখানে সাহানা দেবীর গলায় ‘যদি প্রেম দিলে না প্রাণে’ তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। সেইভাবে ১৯২১ সালে জোড়াসাঁকোয় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে যাবার সুযোগ পেলেন ও সেখানে প্রথম রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে’ আর একলা গলায় গান ‘ আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার’ শুনলেন। শৈলজারঞ্জনের ভাষায় , “ সেইদিন আমার এক জন্মান্তর ঘটল। এতদিন যা ছিল কল্পনায় তা ঘনীভূত হল প্রত্যক্ষতায়। সেদিন আমার দীক্ষা হল রবীন্দ্রনাথের গানে। সেই থেকে আজ এই সুদীর্ঘ জীবনে তা থেকেছে আমার জপমন্ত্র হয়ে, আমার মাঝে আমার সারা জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে”। [ আনন্দবাজার পত্রিকা] আত্মস্মৃতি তে শৈলজারঞ্জন বলেছেন, ‘পরের বছর ১৯২২ সালে আবার বর্ষামঙ্গল হল রামমোহন লাইব্রেরিতে। সেখানে শান্তিনিকেতনের দল গান গাইতে এলেন দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সেসময় আমি এম. এস-সি. পড়ি-বাদুড়বাগান লেনের মেসে থাকি কাছাকাছি-সারাদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে-কোনোমতে গা ঢাকা দিয়ে সেই বর্ষামঙ্গলে একরকম জোর করে ঢুকলাম সব গানগুলি শিখতে চেষ্টা করলাম-বই কিনলাম। তারপরে যখন সভা ভাঙল, তখন যখন বেরিয়ে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথ মোটরগাড়িতে উঠছেন-ভিড় ঠেলে মরণপণ করে, ভিড় ঠেলে গিয়ে ফুটবোর্ডে উঠে ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, তিনি একটু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, একটু আশীর্বাদ করলেন যেন। এই তাঁকে স্পর্শ করলাম আমি প্রথম। প্রথম স্পর্শ করলাম এইদিন। সেদিনের মতো ভরপুর হয়ে আমি হস্টেলে ফিরে গেলাম’।
কলকাতায় ল’ পড়ার সময় শৈলজারঞ্জন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দলে গান গাইতে যেতেন। সেই সময় পাগলাঝোরা অনুষ্ঠানের জন্যে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে এসে কিছু গান শিখিয়েছিলেন, শৈলজা সেই দলে ছিলেন। সেবার রবীন্দ্রনাথ ও রমা করের কাছে তাঁরা তিনটি গান শেখেন – ‘দিনের বেলায় বাঁশি তোমার’, ‘আধেক ঘুমে নয়ন চুমে’ ও ‘নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি’।
ল’ পড়ার সময় প্রভাত গুপ্ত, সুপ্রিয় কর, জ্যোতিষ দত্ত প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা আর গানের আসর বসত। সেখানে শৈলজারঞ্জন ই ছিলেন প্রধান গাইয়ে। বেশির ভাগ সময় আড্ডা হত অরোরা বোর্ডিং নামে একটি মেসে , যেখানে বন্ধুরা থাকতেন।
শৈলজারঞ্জনের অন্যন্য ভাইরাও অনেকেই গাইতে পারতেন। সর্বকনিষ্ঠ ভাই দেবজ্যোতি হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল গানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গসংগীতের তালিম নেন। প্রতিমা এস্রাজ বাজাতে শিখেছিলেন এবং গান গাইতে পারতেন, কিন্তু প্রতিমা বেশিদিন বাঁচেন নি- চার পুত্রকে বেশ ছোটো অবস্থায় রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।
শিক্ষা
শৈলজারঞ্জনের প্রাথমিক শিক্ষা বাহাম গ্রামের পাশের গ্রাম পাইকুরায় গোঁসাইদের পাঠশালায়। পাঠশালার একমাত্র শিক্ষক হৃদয় মাস্টার কে তিনি অতিশয় ভক্তি করতেন। পিতা রমণীকিশোর নেত্রকোণা শহরে ওকালতি করতে শুরু করার পর পুরো পরিবার বাহাম গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন শহরে। শৈলজারঞ্জন ও জেঠতুতো ভাই হেমজারঞ্জন নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময় জ্ঞাতি কাকাদের কাছে তাঁরা প্রথম শান্তিনিকেতনের কথা জানতে পারেন। পিতা শৈলজাকে শান্তিনিকেতনে পাঠানোর পক্ষপাতী ছিলেন না কারণ তখন পড়াশোনার জন্যে শান্তিনিকেতন নাম করেনি। তিনি শৈলজাকে জামতাড়ায় জং বাহাদুর হাই করোনেশন স্কুলে ভর্তি করেন। সেই স্কুল তখন হেডমাস্টার কেশব হাজারীর তত্ত্বাবধানে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো ফল করত। সম্ভবত সেই স্কুলের কথা রমণী কিশোর জানতে পারেন নেত্রকোণার দত্ত হাই স্কুলের সংস্কৃত মাস্টারমশাই এর কাছ থেকে। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন ওঁর টোকুকাকা, রামকৃষ্ণ মিশনের সত্যেন মহারাজ। কলকাতার বহু ছাত্র তখন জামতাড়ার স্কুলে বোর্ডিং এ থেকে পড়াশোনা করত। শৈলজাও এক নম্বর বোর্ডিং এ থেকে পড়াশোনা করতেন। ছোটোবেলা থেকেই শৈলজা তাঁর পিতার মত অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, অল্প সময় পড়ে বিষয়বস্তু মুখস্থ করে নিতে পারতেন। ইংরেজী মাস্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জামতাড়ায় শৈলজারঞ্জন পড়া শেষ করেন নি – কেশব হাজারীর পদত্যাগের পর বহু ছাত্র স্কুল ছেড়ে যায়। শৈলজাকেও স্কুল ছাড়িয়ে নেত্রকোণায় ফেরত নিয়ে আসা হয় ও তিনি দত্ত হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে আই এস সি পড়ার জন্য ভর্তি হন, তখন সারদারঞ্জন রায় ছিলেন প্রিন্সিপাল। প্রথম বছর তাঁদের বাড়িতে থেকে তিনি কলেজ করেন, দ্বিতীয় বছর থেকে বিদ্যাসাগর কলেজের মেসে চলে যান। সেখানেও সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই মাস্টারমশাই শৈলজারঞ্জনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।
আই এস সি পাশ করে শৈলজারঞ্জন স্কটিশ্চার্চ কলেজে বি এস সি পড়ার জন্য ভর্তি হন। সেই সময় গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বাড়িতে শীতল মুখার্জীর কাছে এস্রাজ বাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করেন। বি এস সি পাশ করার পর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজে এম এস সি করেন কেমিস্ট্রীতে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এম এস সি তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়ে আশুতোষ কলেজে কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক হলেন ও স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণার কাজে যুক্ত হলেন। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে পেপার পড়ার সব তৈরী, এমন সময় শৈলজারঞ্জনের মায়ের মৃত্যু হয়। তার পরেই পিতার আদেশ আসে সায়েন্স ছেড়ে ওকালতি পড়তে হবে। অগত্যা শৈলজা কলকাতায় ল’ কলেজে ভর্তি হলেন এবং ওকালতি পাশ করলেন। নেত্রকোণায় গিয়ে কিছুদিন প্র্যাকটিস ও করেছিলেন। এমন সময় শান্তিনিকেতনে কেমিস্ট্রীর অধ্যাপকের পদ খালি থাকায় ডাক পেলেন এবং ১৯৩২ সালে ওকালতি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণে।
শান্তিনিকেতনে আসা
প্রভাত গুপ্ত ১৯৩১ সালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। শৈলজারঞ্জন ল’ পাশ করে নেত্রকোণায় তিন মাস ওকালতি করেন। তারপর পিতা রমণীকিশোর তাঁকে কলকাতায় পাঠালেন উকিলের পোষাক কেনার জন্যে। সেখানে যাবার পরে প্রভাত গুপ্তর বাড়ি দেখা করতে গিয়ে প্রথম শান্তিনিকেতনে যাবার সুযোগ হয়। সেবার প্রভাত গুপ্তর আমন্ত্রণে তিনদিনের জন্য শান্তিনিকেতন দেখে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে শৈলজারঞ্জন সাতদিন সেখানে কাটিয়ে আসেন। দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে খুশি হয়ে ক্লাস বন্ধ করে দিলেন ক’দিনের জন্যে কলকাতা থেকে আসা শৈলজারঞ্জনকে গান শেখানোর জন্যে। সেবার শৈলজারঞ্জন দিনদার কাছ থেকে চোদ্দটি রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন আর নেত্রকোণায় ফিরে গিয়ে সেই গানগুলি দিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।
প্রভাত গুপ্ত খুব ভালো করে জানতেন বন্ধুর রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি আকর্ষণের কথা। তিনি যখন জানতে পারলেন শান্তিনিকেতনের কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গা খালি হবার কথা , তখনই তিনি রথীন্দ্রনাথকে বললেন শৈলজারঞ্জনের কথা। জুন মাসেই শৈলজারঞ্জনের চাকরী ঠিক হয়ে গেল। রথীন্দ্রনাথ শৈলজারঞ্জনকে চিঠিতে জানান তিনি যেন ঢাকায় গিয়ে ডঃ আশুতোষ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আর সেখানে soil Chemistry নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছে সে সম্বন্ধে ভালো করে জেনে আসেন। চাকরী পাবার খবর আসতেই শৈলজারঞ্জন তাঁর পিতাকে জানিয়ে দেন যে ওকালতি আর তিনি করবেন না, তাঁর মনের মতো কাজ তিনি পেয়ে গেছেন।
রথীন্দ্রনাথের চিঠির নির্দেশ মতো শৈলজারঞ্জন শান্তিনিকেতনে এলেন পয়লা জুলাই, যদিও কলেজ খোলার কথা ৬ জুলাই। আসার আগে নির্দেশ মতো তিনি Soil Chemistry সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে এসেছিলেন। বন্ধু প্রভাত গুপ্ত তখনো এসে পৌঁছোননি। সম্ভবত শৈলজারঞ্জন এসে ওঠেন মৃণালিনী পাঠশালার পাশে ‘নতুন বাড়ি’র একটা ঘরে। বন্ধুরা থাকতেন পাশের বাড়িটাতে যার নাম ছিল ‘গৈরিক’। তখন সেখানে দু বাড়ির জলের জন্য একটা কুয়ো ছিল। কলেজ খোলার প্রথম দিন বৈতালিকে গান হল ‘ এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার’ । প্রথমদিকে তাঁর একটু আড়ষ্টতা ছিল কারণ আশ্রমে গুঞ্জন রটেছিল শৈলজারঞ্জন দিনেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের কাছের লোক বলে তাঁর চাকরী হয়েছে। পরে তাঁর অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি অনেকের বন্ধুত্ব লাভ করেন।
প্রথম দু বছরে শৈলজারঞ্জন কেমিস্ট্রী পড়ানোর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নানান কার্যকলাপে উৎসাহভরে যোগ দেন। হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল শেখেন হেমেন্দ্রলাল রায়ের ক্লাসে, বচ্চন মিশ্রর কাছে সারেঙ্গীর তালিম নেন, কলাভবনে আঁকার ক্লাসও করেন । ‘দৈগন্তিক’ বাড়িতে নবাগতদের আসর বসত, সেখানে তিনি গান গাইতেন, এবং সহকর্মীদের অনেককে গান শেখাতেনও (ক্ষিতিশ রায়, জ্যোৎস্নানন্দ রায় প্রমুখ)। রসায়নের গবেষণাগার তৈরী করার কাজে তাঁর অবদান অনেক। উদয়নে বর্ষাসঙ্গীতের আসরে একক গান গাইলেন ‘গগনে গগনে আপনার মনে’ গুরুদেবের সামনে, প্রশংসাও পেলেন। তবে গাইয়ে হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্খা তাঁর ছিল না, গান শিখতে ও বন্ধুদের শোনাতে, শেখাতে পেরেই তিনি খুশি ছিলেন বরাবর। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরেই ‘রথের রশি’র রূপান্তর নাটক ‘কালের যাত্রা’ তে এবং পরের বছর ‘বৈকুন্ঠের খাতা’ নাটকে বিপিনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে গেলেন লখনৌ সঙ্গীত সম্মেলন, দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে দল নিয়ে গেলেন বোম্বে, পরের বছর গুরুদেবের সিংহল যাত্রায় নৃত্যগীতের দলেও তিনি সামিল হলেন। এই সময়েই স্বরস্থান অভ্যাস করে ও দিনেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে নিজের চেষ্টায় তিনি আকারমাত্রিক স্বরলিপি তৈরী করা আয়ত্ত্ব করেন ও দিনেন্দ্রনাথেরই উৎসাহে তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ‘মম মন উপবনে’ প্রবাসী পত্রিকায় ( ১৯৩৪ সালে) মুদ্রিত হয়। আশ্রমে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈতালিকের দল তৈরী করে তাদের নতুন নতুন গান শিখিয়ে বৈতালিক করানো ছিল তাঁর খুব প্রিয় কাজ। এইভাবে বহিরাগত শৈলজারঞ্জন ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে গুরুদেবের কাছাকাছি নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। চীনভবনের পাশে নীচুবাংলার বাড়িতে শৈলজারঞ্জন অনেকদিন কাটিয়েছেন। সেখান থেকে পরে তিনি চলে যান পূর্বপল্লীতে।
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা
১৯৩৫ সালে দিনেন্দ্রনাথ আশ্রম ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যান। তখন কিছুদিন শৈলজারঞ্জনের গান শেখা বন্ধ থাকে। তারপর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে ডেকে নেন গান শেখাবার জন্য। এরপর থেকে নিয়মিত গুরুদেবের কাছে তিনি গান শেখেন , দুশোর বেশি গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন, স্বরবিতান সম্পাদনা করেন। গুরুদেবের কাছে এই পর্বে শেখা তাঁর প্রথম গান হল ‘পথহারা তুমি পথিক যেন গো’। পরে ফিল্মের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুমোদন করার ভারো তাঁকে দেন রবীন্দ্রনাথ। কলকাতায় শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে গুরুদেবের নির্দেশক্রমে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান করান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘গীতাম্বুধি’। তাঁর জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে উপহার দেন –
জন্মদিন এল তব আজি
ভরি লয়ে সংগীতের সাজি ।
বিজ্ঞানের রসায়ণ রাগরাগিণীর রসায়ণে
পূর্ণ হল তোমার জীবনে ।
কর্মের ধারায় তব রসের প্রবাহ যেথা মেশে
সেইখানে ভারতীর আশীর্বাদ অমৃত বরষে।
গুরুদেবের সঙ্গে শৈলজারঞ্জনের সম্পর্ক ছিল অনেকটা গুরু শিষ্য ও খানিকটা বন্ধুর মতো। গুরুর বয়েস পঁচাত্তর আর শিষ্যের পঁয়ত্রিশ। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত গুরুদেবের গানের ভাণ্ডার রক্ষার ভার অনেকটাই ছিল তাঁর ওপর। অনেক গান তিনি গুরুদেবকে অনুরোধ বা খানিকটা আবদার করে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে হল বর্ষামঙ্গলের জন্যে লিখিয়ে নেওয়া ষোলটি গান। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে অনুষ্ঠিত শেষ বর্ষামঙ্গল। অনেক সময় গুরুদেবের গানের স্বরলিপি করার সময় দেখেছেন গুরুদেব দুরকম সুর দিয়েছেন – তিনি দুরকম সুরই সুরান্তর হিসেবে স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন। এমনো হয়েছে যে দিনেন্দ্রনাথের কাছে শেখা গান রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অন্যরকম সুরে শিখিয়েছেন ও বলে দিয়েছেন সে গানটি যেন তাঁর শেখানো সুরেই গাওয়া হয়। শৈলজারঞ্জনের মতে গুরুদেবের জীবিতকালে করা স্বরলিপি পরবর্তীকালে অনেক বদলে গেছে এবং বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করেনি। গ্রামোফোন রেকর্ডে অনেকসময় শিল্পীরা অরাবীন্দ্রিক গায়কীতে ও ত্রুটিপূর্ণ সুরে গেয়েছেন ও তার থেকে সাধারণ শিল্পীরা সেই গানই গলায় তুলে নিয়েছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ২০০০ সালে কপিরাইট উঠে গেলে গুরুদেবের ইচ্ছা অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার প্রতি আর দায়বদ্ধতা কারুর থাকবে না।
গুরুদেব অনেক সময়েই শৈলজারঞ্জনের বাঙাল ভাষার ঝোঁক নিয়ে রসিকতা করতেন, শৈলজারঞ্জন সমানে সমানে উত্তর দিতেন। অনেক সময় গুরুদেব শৈলজারঞ্জনকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইতেন যে তিনি রসায়ণের চেয়ে গানকেই বেশি ভালোবাসেন। তাঁর কথায়- ‘তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কী পড়াও , তুমি বলবে কেমিক্যাল মিউজিক বা মিউজিক্যাল কেমিস্ট্রী’।
শৈলজারঞ্জন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে শেখা অনেক গানের সুর হুবহু মনে রেখেছিলেন যা স্বরলিপির বিভিন্ন মুদ্রণের ফলে অনেক সময় বদলে গিয়েছিল। সেই সুরান্তরগুলি তাঁর কিছু ছাত্র ছাত্রী ও আত্মীয়জনের কাছে টেপ রেকর্ডারে ধরা আছে। এই সুরগুলি অবিলম্বে স্বরলিপি করে বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়া দরকার।
সংগীতভবনের দায়িত্ব
১৯৩৯ সালে রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন কর শৈলজারঞ্জনকে একান্তে ডেকে প্রস্তাব দেন সংগীতভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে। শৈলজারঞ্জন এই দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলেন ইন্দিরা দেবীকে ডেকে এই ভার তাঁকে দিতে। গুরুদেব তখন বলেছিলেন, ‘তুমি বিবির কথা বলছ? আমি অমিতার কথাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমার আর সময় নেই। … তোমরা যে বাংলা বা বিজ্ঞানের ক্লাস নাও, সে আমার নয়। কলাভবনে যে আঁকার ক্লাস হয় সেটা নন্দলালের – আমার নয়। সংগীতভবনে আমার গান আমার নাটক – সে আমি কার হাতে দিয়ে যাব? তুমি ভার নিলে আমি নিশ্চিন্ত হব। …… তুমি আমাকে তো মানো? তাহলেই হবে। আমাকে জিজ্ঞেস করে কাজ চালিয়ে নেবে’।
তখন রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভালো নয়। শৈলজারঞ্জন না করতে পারলেন না, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থেকেই গেল। যদি গুরুদেবের নিজের সৃষ্টি ঠিকভাবে রক্ষা করার যোগ্যতা না থাকে তবে কি হবে। তিনি ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর সাহায্যে এই মর্মে পত্র লিখিয়ে নিলেন যে দু পক্ষেরই পিছিয়ে আসার উপায় থাকবে। শৈলজারঞ্জন প্রথমে রসায়নের ক্লাস নেবেন ও তার সঙ্গে সংগীতভবনের দায়িত্ব সামলাবেন – দরকার হলে আবার পুরোপুরি রসায়ন বিভাগে ফিরে আসবেন। বলা বাহুল্য এই চিঠি ছাড়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বলে কিছু তখন তাঁকে দেওয়া হয়নি – সে প্রথাও তখন অবশ্য- প্রচলিত ছিল না।
এরপর দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি সংগীতভবনের দায়িত্ব সামলেছেন। প্রথম কয়েক বছরে সংগীতভবনের পাঠক্রম, সময় তালিকা ( timetable), পরীক্ষা ও ডিগ্রীলাভের ব্যবস্থা করেছেন এবং এই সময়ে আগের অনেক প্রথা ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে। এতে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বাধা আপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে – বিশেষ করে স্বরলিপি শিক্ষা আবশ্যিক করা ও পরীক্ষার প্রবর্তন করার কাজে। কলকাতায় উচ্চশিক্ষালাভ করার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চালনা পদ্ধতির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত তো ছিলেন, তার সঙ্গে গুরুদেবের সংগীত ও নাটকের শুদ্ধতা রক্ষার কথা মাথায় রেখেই কাজ করতে হয়েছে। রাগসংগীত শিক্ষা, এস্রাজ বাজানো, ঋতু পরিবর্তন ও শান্তিনিকেতনের উৎসবের সঙ্গে মানিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের তালিকা বানানো, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের পাঠক্রম নির্দিষ্ট করা, ঠিক সময়ে ক্লাস নেওয়া এবং তার সঙ্গে উৎসবের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নাচ ও গানের তালিম দেওয়া – সব তাঁর নজরে ছিল।
গুরুদেবের মৃত্যুর পর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কিছুকাল বিশ্বভারতীর প্রনেত্রী হিসেবে আশ্রমে ছিলেন এবং সংগীতভবনের তত্ত্বাবধান ও করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে একত্রে অনেক কাজ করেছেন শৈলজারঞ্জন। ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে প্রচুর গানের স্বরলিপি পেয়ে সেগুলি প্রকাশ করেছেন, এখান ওখান থেকে আরো অনেক রবীন্দ্রসংগীত জোগাড় করেছেন যার স্বরলিপি ছিল না, শুধু মুখে মুখে চলত। ‘ভানুসিংহের পদাবলীর’ নৃত্যনাট্য রূপ প্রস্তুত করেছেন তিনি ইন্দিরা দেবী এবং নন্দিতা কৃপালনী একসঙ্গে, যা এখন শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৫৬ সালের পর থেকে অনেকবার শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের দল নিয়ে বার্মা ( মায়ানমার) তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, করিয়েছেন। বার্মার ছাত্রছাত্রীদের নাচ শিখিয়ে তাদের দিয়ে নৃত্যনাট্যে সখীদের নাচ করিয়েছেন। কাশ্মীরে যুবরাজ করণ সিংহের আমন্ত্রণে গিয়ে চিত্রাঙ্গদা ও ভানুসিংহের পদাবলী করিয়েছেন। এ ছাড়া দেশের নানা জায়গায় গিয়ে স্থানীয় লোকেদের উৎসাহ দিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। কালিম্পং এ ‘ চিত্রভানু’ তে ‘Women’s Arts and Crafts Training Centre’ এ গিয়ে এক মাস ছিলেন, তখন তার প্রধান শিক্ষিকা ভগিনী নন্দিতা সেন মজুমদারের অনুরোধে বেশ কয়েকজন নেপালী মেয়ের গান ও নাচের পরীক্ষা নিয়ে তাদের সংগীতভবনে ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন উপাচার্য পদের বদল হয়েছে অনেকবার। সত্যেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন বিজ্ঞানের লোক, তিনি শৈলজারঞ্জনকে খুব পছন্দ করতেন। ১৯৫৯ সালে একবার শৈলজারঞ্জন যখন পদত্যাগ করেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে পুনর্বহাল করেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে সুধীরঞ্জন দাশের সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনান্তর ঘটায় তাঁর প্রাণের শান্তিনিকেতন আশ্রম ও সংগীতভবন ছেড়ে তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে চলে যান – গুরুদেবের শতবর্ষ পূর্তির উৎসবে শান্তিনিকেতন তাঁর অভাব অনুভব করেছে।
পারিবারিক জীবন
শৈলজারঞ্জন রা ছিলেন সাত ভাই ও এক বোন। তাঁদের নাম যথাক্রমে শৈলজারঞ্জন, গিরিজারঞ্জন, সুবোধরঞ্জন, প্রতিমা, নীরদরঞ্জন, প্রবোধরঞ্জন, অমলরঞ্জন এবং দেবজ্যোতি। ভগিনী প্রতিমার বিবাহ হয় ময়মনসিংহের নামকরা উকিল শৈলেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। এম এস সি পাশ করার পর শৈলজারঞ্জনের বিবাহ হয় আসামের মন্ত্রী রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যা অমিয়া দেবীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা ও রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগিনী। কিন্তু বিবাহের জীবন স্থায়ী হয়নি। স্ত্রী অমিয়া দেবী বাপের বাড়ি চলে যাবার পর নিজে থেকে ফিরে আসেন নি আর শৈলজারঞ্জনের দিক থেকে হয়তো যথেষ্ট তাগিদ ছিল না। এর ফলস্বরূপ শৈলজারঞ্জন সমস্ত মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন রবীন্দ্র সাহচর্য ও রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়। অমিয়াদেবীর ভগিনী অমলা (কুইনি) র সঙ্গে শৈলজারঞ্জনের যোগাযোগ ছিল, এবং তিনি শান্তিনিকেতনে সুগায়িকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অমিয়াদেবী পরবর্তীকালে কলকাতায় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগ দেন। শৈলজারঞ্জন তাঁর খোঁজ রাখতেন। অমিয়াদেবীর মৃত্যুর পর শৈলজারঞ্জন তাঁর শ্রাদ্ধ করেন অমলরঞ্জনের সল্ট লেকের বাড়িতে।
শান্তিনিকেতনে চাকরীরত অবস্থায় তিনি পরিবারের অনেককে সেখানে আনিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র বোন প্রতিমার চতুর্থ পুত্র বলেন্দ্রনাথ, ভাই গিরিজারঞ্জনের পুত্র অমেয়, কন্যা নবনীতা – সবাই তাঁর নীচুবাংলার বাড়িতে থাকতেন ও সেখানে পড়াশোনা করতেন। পরে শৈলজারঞ্জনের মামা সুরেশচন্দ্র সেন মজুমদারের পরিবারও তাঁর কাছে এসে ওঠেন। এই পরিবারের সবাই শান্তিনিকেতনেই পড়াশোনা ও চাকরী করেন ও নিজেদের বাড়ি করে সেখানে আজীবন সেখানে থেকে যান। গিরিজারঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তীকে শৈলজারঞ্জন কলাভবনে হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেন, কিন্তু বাসন্তীদেবী খুব অল্পদিনের মধ্যেই রোগভোগের পর মারা যান। শৈলজারঞ্জনের আরেক ভাই প্রবোধরঞ্জন শান্তিনিকেতনে কলেজে পড়াশোনা করেন। ছোট ভাই দেবজ্যোতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুত্তমা ছোটবেলা থেকে শান্তিনিকেতনে আবাসিক ছাত্রী হিসেবে থেকে এম এ পাশ করেন। শৈলজারঞ্জনকে বিশ্বভারতী থেকে পূর্বপল্লীতে একটি লীজের বাড়ি দেওয়া হয়, সেখানে তিনি অবসরের পর এসে থাকতেন। সেই বাড়িটিতে তাঁর সেজ ভাই নীরদরঞ্জন অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এসে সপরিবারে বাস করতে শুরু করেন।
শান্তিনিকেতন থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেবার পর শৈলজারঞ্জন কলকাতায় গড়পারের বাড়িতে এসে ওঠেন। সেখানে রোজ অনেক ছাত্রছাত্রীর ভীড় হতে থাকায় তখনকার সি আই টির প্রধান শ্রী করুণাকেতন সেন এন্টালি পদ্মপুকুর এ সি আই টি বিল্ডিং এ একটি ছোট ফ্ল্যাট এর ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে তিনি তাঁর ছোটো ভাই দেবজ্যোতি ও তাঁর স্ত্রী নমিতার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। সেই বাড়িতে তিনি পনেরো বছরেরও বেশিদিন ছিলেন, তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন কাজী নজরুলের পরিবার ও শিল্পী সুধীর খাস্তগীরের পরিবার। ভ্রাতৃবধূ নমিতা তাঁর প্রতিদিনের দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন। রোজ দশটা থেকে গানের ক্লাস বসত, অনেক শিল্পীরা ও ছাত্রছাত্রীরা ওঁর ছোট্ট ঘরে বসে এস্রাজের সঙ্গে সুর মেলাতেন।
শৈলজারঞ্জনের নিজের পরিবার না থাকায় তিনি আত্মীয়স্বজন ও ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ঘুরে ঘুরে থাকা পছন্দ করতেন এবং সবাই তাঁকে রাখতে পেরে ধন্য হতেন। স্থায়ীভাবে তিনি থেকেছেন পদ্মপুকুর সি আই টি বিল্ডিং এ, তারপর কনভেন্ট রোডের তিনতলার ঘরে ভাই প্রবোধরঞ্জনের পরিবারের সঙ্গে, কেষ্টপুরের বাগানবাড়িতে ও সবশেষে সল্ট লেকের এ ডি ২৭৬ এ – ভাই অমলরঞ্জন ও ভ্রাতৃবধূ কমলার তত্ত্বাবধানে। মাঝে মাঝেই চলে যেতেন বোনপোদের বাড়িতে – যেমন বলেন্দ্রনাথের ইছাপুরের বাড়িতে, জ্যোতিরিন্দ্রের দুর্গাপুরের বাড়িতে, বা নৈহাটিতে অবনীন্দ্রের বাড়িতে। যেখানেই যেতেন সেখানে গানের আসর বসে যেত, শেখার জন্যে ভীড় জমে যেত, আর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে গান শেখাতেন। বাড়িগুলি ‘গানের বাড়ি’ নামে পরিচিত হয়ে যেত। তিনি তাঁর ছাত্রীদের বাড়িতেও যেতেন, বিশেষ করে কে সি দাসের পরিবারের মেয়ে মঞ্জুলিকা দাশের বাড়িতে। সেখানে প্রতি সপ্তাহে তাঁর গানের ক্লাস বসত । সবার কাছে তিনি অত্যন্ত ‘ disciplined’ মানুষ হলেও নাতি নাতনীরা ছিল ভারি আদরের। বড়োরা যেমন ওঁকে সমীহ করে চলত , বাচ্চারা তেমন ওঁকে স্নেহময় দাদু হিসেবে যা খুশি আবদার করত।
যদিও ছাত্রছাত্রীরাই তাঁর প্রাণ ছিল, তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যরাও তাঁর কাছে গান শেখার ও অনুষ্ঠানে গান করার সুযোগ পেয়েছে, যেমন ভ্রাতৃবধূ নমিতা, ভাইঝি অনুনীতা, অনুত্তমা, অনুষঙ্গা, নাতনী অমৃতা, অনমিত্রা। পরিবারের অনেকেরই গানের সুন্দর গলা ছিল কিন্তু সবাইকে তিনি সামনে আনেন নি। বোনপো অবনীন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্র গানের স্কুল তৈরী করেছিলেন, তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের অনেকেই এস্রাজ বাজাতে পারতেন যেমন মামা সুরেশচন্দ্র, তাঁর ছেলে সুব্রত সেন মজুমদার। সুরেশচন্দ্রের নাতি শুভায়ু তাঁর ধারা বজায় রেখে এস্রাজ বাজানোকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন।
পরিবারের সবার পাশে থাকতে ভালোবাসতেন এবং প্রায় সব পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বিয়েতে উপস্থিত থাকতেন। পঁচাশি বছর বয়েসে নীরনরঞ্জনের কনিষ্ঠ পুত্র অতনুর বিবাহে দুর্গাপুর গিয়েছিলেন বরকর্তা হয়ে।
পরিবারের অনেকের নামকরণ তিনি করেছেন , যেমন অনুত্তমা, অনুষঙ্গা, নীপমিতা, অনুনীতা। তাঁর অনুরোধে গিরিজারঞ্জনের দুই পুত্র কন্যার নাম দেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ – অমেয় ও নবনীতা। তাঁর জীবন ছিল এক নিরাসক্ত সাধকের মত – কিছু পার্থিব জিনিসের প্রতি তাঁর মায়া ছিল না। এমনকি গুরুদেবের কাছ থেকে পাওয়া চিরকুট বা চিঠিও খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে রাখা ছিল না।
শেষ জীবনে বেশ কয়েকটি বছর শৈলজারঞ্জন ছিলেন ভাই অমলরঞ্জনের সল্ট লেকের AD 276 এর বাড়িতে। কমলার সঙ্গে তাঁর অনেক গল্প হত, আবদার করতেন তাঁর জন্যে সোয়েটার বানিয়ে দেবার। সল্ট লেকের বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর জবানিতে আত্মকথা ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’ বই হয়ে প্রকাশিত হয়, সেটি অনুলেখন করেন প্রবোধরঞ্জনের স্ত্রী সবিতা দত্ত মজুমদার। এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আসা যাওয়া করতেন। এখানেই তিনি ১৯৯২ সালে বিরানব্বই বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।
রামকৃষ্ণ পরমহংসর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি প্রার্থনা গীতে সুর সংযোজন করেন। তাদের একটি এস্রাজ দান করেন যেটি সেখানে সযত্নে রাখা আছে।
কলকাতার কর্মজীবন
শান্তিনিকেতনে থাকার সময় থেকেই শৈলজারঞ্জন কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধভাবে প্রচার ও শিক্ষার প্রসারের কথা ভেবেছিলেন। ‘গীতবিতান’ ছিল শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম প্রথাগতভাবে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান – এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শুরু থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন। ‘গীতবিতান’ এর প্রধান ছিলেন নীহারবিন্দু সেন এবং গীতা সেন। শুভ গুহ ঠাকুরতার ‘দক্ষিণী’ সংস্থার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন প্রথম দিকে। ‘সুরঙ্গমা সংগীত শিক্ষায়তন’ এর মূল ব্যক্তি ছিলেন তিনি এবং প্রভাস নিয়োগী, এর গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ১৬ আগস্ট নেতাজী ভবনে। স্বেচ্ছাঅবসর নেবার পর কলকাতায় এসে তিনি সুরঙ্গমাকে মনের মত করে গড়ে তোলেন, তার পাঠক্রম তৈরী করেন শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের আদলে। সেখানে শুধু এস্রাজ ও তানপুরার সাহায্যে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হত। সেই সময় তিনি ‘রবিরঞ্জনী’ নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন প্রধানত সমবেত কন্ঠে গান গাওয়াবার জন্য। সেখানে উৎপল, আশিস ভট্টাচার্য, বুলবুল বসু, বুলবুল ভট্টাচার্য, নমিতা দত্ত মজুমদার, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত প্রমুখ ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করিয়েছেন। সুরঙ্গমায় নৃত্য শিক্ষিকা পূর্ণিমা ঘোষকে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে যথাযথ নৃত্যে তালিম দিয়ে, শান্তিনিকেতন থেকে শিক্ষক আনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তৈরী করিয়েছেন শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, মায়ার খেলা নৃত্যনাট্য পরিবাশন করার জন্যে। অনেক বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে পাটনা রবীন্দ্রভারতীতে যেতেন গান শেখাতে, সেখানেও নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেছেন।
সুরঙ্গমাতে শৈলজারঞ্জন সপ্তাহে একদিন ‘স্পেশাল’ ক্লাস নিতেন কঠিন টপ্পা অঙ্গের গান শেখানোর জন্য। তাঁর শিল্পী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, মায়া সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা ঘটক, ঊর্মিলা ঘোষ, আশিস ভট্টাচার্য, বুলবুল বসু, বুলবুল সেনগুপ্ত, প্রসাদ সেন প্রমুখ।
সুরঙ্গমার সল্ট লেক শাখা শুরু হয় শৈলজারঞ্জনের জীবৎকালেই । সেই শাখায় রাসবিহারীর সুরঙ্গমা থেকে পাশ করা ছাত্রীরা গান শেখাতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন রীণা মুখোপাধ্যায়, অনুনীতা বসু, কুমকুম মিত্র, অমলেন্দু সাঁই, অনুষঙ্গা গুপ্ত প্রমুখ। দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার ছিলেন দুই সুরঙ্গমার হিন্দুস্তান ক্লাসিক্যাল এর প্রধান শিক্ষক। ফাইনাল পরীক্ষা অবশ্য রাসবিহারীর সুরঙ্গমাতেই হত। পরবর্তীকালে রীণা চট্টোপাধ্যায় গীতবিতান প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।
বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি দস্তিদার প্রমুখ। শৈলজারঞ্জন দেখেছিলেন অনেক স্বরলিপি যেগুলি গুরুদেবের আমলে তৈরী হয়েছিল ওঁর অনুমতি নিয়ে, সেগুলি আবার করে সদস্যদের কাছে পাঠানো হত কোনো পরিবর্তন করা হবে কিনা জানার জন্যে। শৈলজারঞ্জন আপত্তি জানিয়েছিলে এই পদ্ধতির, কারণ ওঁর মত ছিল যে স্বরলিপি গুরুদেব অনুমোদন করে গেছেন সেগুলি আবার করে অনুমোদনের অপেক্ষা রাখেনা। এই সময় উনি আকাশবাণীতে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে হারমোনিয়ামের ব্যবহার নিয়েও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই ব্যপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতনে ছাত্রী থাকার সময় শৈলজারঞ্জন ছিলেন সংগীতভবনের দায়িত্বে – সে সুবাদে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা।
রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধ সুর ও গায়কী রক্ষা করার জন্যে সারাজীবন শৈলজারঞ্জন লড়াই করে গেছেন। যেখানেই ওঁকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করা হয়েছে সেখানে উনি রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে তাঁর গান গাইতে বলেছেন, তাঁর কোন বিষয়ে গায়ক স্বাধীনতা নিতে পারেন বা পারেন না – সে ব্যপারে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ব্যবস্থাপনায় শৈলজারঞ্জন এ রাজ্যের ও বাংলাদেশের রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকদের সম্মেলন করেছিলেন – যেখানে শুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্মেলনের প্রস্তাব তেমন কার্যকরী হয়নি। বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি শৈলজারঞ্জনের সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন – যেমন অরুণ ভট্টাচার্য, গৌরী আইয়ুব, সুবিনয় রায়, বুলবুল বসু – সেই সাক্ষাৎকার গুলিতে শৈলজারঞ্জনের নিজের জীবন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।
জীবন সায়াহ্ন
শেষ জীবনে শৈলজারঞ্জন তাঁর ভাই অমলরঞ্জনের কেষ্টপুরের বাগানবাড়িতে থাকা স্থির করলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর অমলরঞ্জন সল্ট লেকে নতুন বাড়ি তৈরী করলেন, তখন শৈলজারঞ্জন তাঁদের সঙ্গে সল্ট লেক এ ডি ২৭৬ এর বাড়িতেই বাকি জীবন কাটাতে চলে এলেন। এখানে আসার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই অমলরঞ্জন ও তাঁর পুত্র অভিজিৎ এর দেহাবসান হয়। অমলরঞ্জনের স্ত্রী কমলা দত্ত মজুমদার তাঁর ভাশুরের দেখাশোনার ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। এই বাড়িতে শৈলজারঞ্জনের দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হয়েছে, সুরঙ্গমার ক্লাস হয়েছে, শৈলজারঞ্জনের ভাইয়ের মৃত্যুর পর স্মরণসভা হয়েছে শৈলজারঞ্জনেরই তত্ত্বাবধানে। শৈলজারঞ্জনের নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ফলে দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন, এবং অনেকদিন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়ে গেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির দৌলতে নব্বই বছর বয়েসেও বলে দিতে পারতেন কোন স্বরবিতানের কোন পাতায় কোন গানটি খুঁজতে হবে। বয়সোচিত কারণে যখন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মেডিক্যাল বোর্ড বসায় তাঁর চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার যখন গান শেখানো বারন করে দিলেন তখন তাঁর অনুরোধে তাঁর প্রিয় ছাত্র আশিস ভট্টাচার্য ঐ বাড়িতে গানের ক্লাস নিতে শুরু করেন, যাতে শৈলজারঞ্জন রবীন্দ্রসংগীত শোনার থেকে বঞ্চিত না হন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ ডকুমেন্টারী ফিল্ম ‘মোহর’ তৈরীর জন্যে শৈলজারঞ্জনের সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন।
প্রতিদিন বহু ছাত্রছাত্রী ও গুণমুগ্ধ লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এই বাড়িতেই ১৯৯২ সালে ২৪ শে মে বিরানব্বই বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। তখন তাঁর ভাইদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন গিরিজারঞ্জন ও দেবজ্যোতি। এঁরা দুজনেই ১৯৯৪ সালে মারা যান।
References
১। যাত্রাপথের আনন্দগান – শৈলজারঞ্জন মজুমদার – আনন্দ পাবলিশার্স
২। রবীন্দ্রসংগীতচিন্তা – শৈলজারঞ্জন মজুমদার – পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
৩। নানাজনের শৈলজারঞ্জন – সম্পাদনা অনুত্তমা ঘোষ – বীরুতজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী
৪। অগ্নিরক্ষার এক ঋত্বিক – আলপনা রায়
৫। আচার্যের আশীর্ভাষণ অগ্নিরক্ষা – আশ্রমিক সংঘ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা
৬। যাত্রাপথের আনন্দে সঙ্গীত রসায়ণ – সোমনাথ চ্যাটার্জী
৭। রবীন্দ্রসংগীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার শতবর্ষ উদযাপন – সুরঙ্গমা শিক্ষায়তন